ক্ষমতা কমছে প্রধানমন্ত্রীর, নিয়োগ ক্ষমতা বাড়ছে রাষ্ট্রপতির
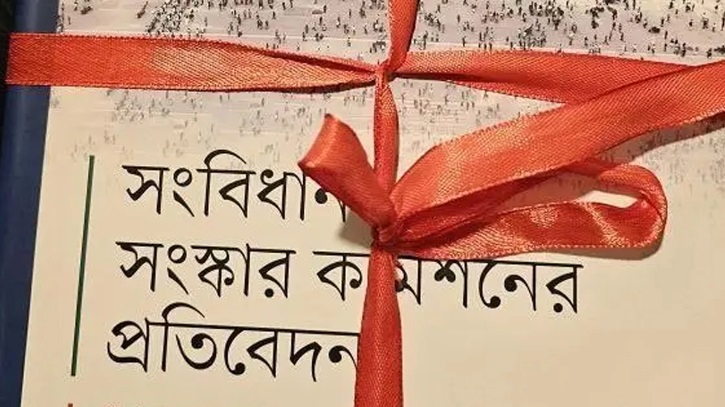
ছবি: সংগৃহীত
বাংলাদেশের বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামোতে প্রধানমন্ত্রীর হাতে নির্বাহী ক্ষমতার ব্যাপক কেন্দ্রীকরণ দীর্ঘকাল ধরে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের সমালোচনার বিষয়।
আগস্ট ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের পর গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই ক্ষমতা কাঠামোতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন (সিআরসি) এবং পরবর্তীতে রাজনৈতিক ঐকমত্যের জন্য জাতীয় ঐকমত্য কমিশন (এনসিসি) গঠন করে।
এই কমিশনগুলোর মূল প্রস্তাবনা ছিল প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র ক্ষমতা হ্রাস করা এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।
আলোচনা ও মতবিনিময়ের পর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: একজন ব্যক্তি জীবনে সর্বোচ্চ ১০ বছর প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে পারবেন; সরকারি দল, বিরোধী দল ও বিচার বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত বাছাই কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন (ইসি) গঠিত হবে; এবং অর্থবিল ও আস্থা ভোট ছাড়া অন্য যেকোনো বিষয়ে সংসদ সদস্যরা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবেন।
তবে সংস্কারের মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য অপরিহার্য বেশ কিছু মৌলিক প্রস্তাবে বিএনপিসহ কয়েকটি দল ভিন্নমত (নোট অব ডিসেন্ট) দিয়েছে।
এর মধ্যে রয়েছে: সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগের জন্য জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি) গঠন, একই ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধানের পদে না থাকা, এবং সংসদের উচ্চকক্ষে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতি। বিএনপি-এর যুক্তি হলো, এসব প্রস্তাব কার্যকর হলে নির্বাহী বিভাগ দুর্বল হয়ে যাবে এবং সরকারের কর্তৃত্ব থাকবে না।
এই ঐকমত্য ও ভিন্নমতের বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যতটুকু ঐকমত্য হয়েছে, তাতে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা খুব সামান্যই হ্রাস পাবে। সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য—অর্থাৎ ক্ষমতার প্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণ—সম্পূর্ণভাবে সফল হবে না।
যেসব মৌলিক প্রস্তাবে ভিন্নমত রয়েছে, তা ভবিষ্যতে কোনো নির্বাচিত সরকার, বিশেষত বিএনপি ক্ষমতায় এলে, বাস্তবায়নের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এই বাস্তব পরিস্থিতি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রব্যবস্থার গতিপথ নিয়ে এক গভীর অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে।
এই প্রতিবেদনটি বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামো, প্রস্তাবিত সংস্কার, রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান এবং তার সম্ভাব্য প্রভাবের একটি বিশদ ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রদান করে।
ভূমিকা: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সংস্কারের অপরিহার্যতা
আগস্ট ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থান ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা, যা দেশের শাসনব্যবস্থায় দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং জবাবদিহিতার অভাবের বিরুদ্ধে জনগণের একটি স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহের প্রতিফলন। এই অভ্যুত্থান কেবল রাজনৈতিক পরিবর্তনই আনেনি, বরং একটি গণতান্ত্রিক, জবাবদিহিমূলক এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে ।
এই প্রেক্ষাপটে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক অধ্যাপক আলী রীয়াজকে প্রধান করে একটি ৯ সদস্যের সংবিধান সংস্কার কমিশন (CRC) গঠন করে, যার ম্যান্ডেট ছিল বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রদান করা। কমিশনের লক্ষ্য ছিল জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, জনগণের ক্ষমতায়ন, এবং ক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা । এই কমিশন তাদের সুপারিশমালা পেশ করার পর, সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি জাতীয় ঐকমত্য কমিশন (NCC) গঠন করে, যার মূল দায়িত্ব ছিল সাংবিধানিক সংস্কারের প্রস্তাবনাগুলো নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপের মাধ্যমে একটি কার্যকর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা ।
পর্যবেক্ষকরা বলছেন, সংবিধান সংস্কারের মতো একটি মৌলিক ও স্পর্শকাতর বিষয়কে দুইটি ভিন্ন স্তরে প্রক্রিয়াকরণের সিদ্ধান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত পদক্ষেপকে নির্দেশ করে। প্রথমত, সংবিধান সংস্কার কমিশন দ্বারা আদর্শিক ও বিশেষজ্ঞ মতামতভিত্তিক সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়। এরপর জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সেই সুপারিশগুলোকে রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্যতা ও বাস্তবসম্মত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। এই দ্বৈত প্রক্রিয়া ইঙ্গিত দেয় যে, সরকার একটি নিখুঁত আদর্শিক সংস্কারের পরিবর্তে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি কার্যকর আপোষ প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী ছিল। তবে এই পদ্ধতি একটি সম্ভাব্য দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়: যদি আদর্শগতভাবে অপরিহার্য কোনো প্রস্তাব রাজনৈতিক আপোষের কারণে বাতিল হয়ে যায়, তাহলে সংস্কারের মূল লক্ষ্য কতটা সফল হবে? এই প্রতিবেদনটি এই প্রশ্নটির গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণ করবে।
বিদ্যমান সাংবিধানিক ক্ষমতা কাঠামো: প্রধানমন্ত্রীর এককেন্দ্রিক কর্তৃত্ব
বাংলাদেশের সংবিধান সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা অনুসরণ করে। তত্ত্বগতভাবে, এটি ক্ষমতাকে আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে বিভাজন করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলে। তবে বাস্তবে, সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রায় সমস্ত নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে কেন্দ্রীভূত। সংবিধানের ৫৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, "প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এ সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে" । যদিও রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান এবং সর্বোচ্চ পদাধিকারী , তিনি কেবল প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সকল দায়িত্ব পালনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য ।
এই ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের ফলস্বরূপ, সাংবিধানিক ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদগুলোতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রীর একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার, সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যান ও সদস্যসহ গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিলেও, এই নিয়োগের জন্য প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক। এর ফলে এসব প্রতিষ্ঠানে কার্যত প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে, যা তাদের নিরপেক্ষতা ও কার্যকারিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।
ক্ষমতার এই ভারসাম্যহীনতাকে আরও সুসংহত করেছে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ। এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কোনো সংসদ সদস্য যদি সংসদে দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দেন, তবে তার সংসদ সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়। এই বিধানটি সংসদকে কার্যত একটি রাবার স্ট্যাম্পে পরিণত করেছে, যেখানে বিরোধী দলসহ কোনো সংসদ সদস্যই সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন না। ফলস্বরূপ, প্রধানমন্ত্রীর হাতে সরকার, সংসদ ও দলের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বিশ্বের অন্যান্য সংসদীয় গণতন্ত্রের সরকার প্রধানদের তুলনায় অনন্যভাবে কেন্দ্রীভূত।
একজন বিশেষজ্ঞ যেমন বলেছেন, কোনো নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোয় কোনো নিয়ন্ত্রণবিহীন এমন ক্ষমতার অধিকারী অন্য কোনো কর্মকর্তা বিশ্বে দেখা যায় না।
এই ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ কেবল সাংবিধানিক বিধানের ফল নয়, বরং একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতিরও প্রতিফলন, যেখানে দলীয় প্রধানের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করার কোনো সুযোগ নেই। যখন সংসদীয় প্রক্রিয়ায় বিরোধিতার কোনো কার্যকর সুযোগ থাকে না, তখন বিরোধী শক্তি রাজপথে আন্দোলনকে একমাত্র বিকল্প হিসেবে বেছে নেয়, যা দেশের গণতন্ত্র ও স্থিতিশীলতার জন্য একটি বড় হুমকি।
সংস্কার কমিশনের মূল প্রস্তাবনা: ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার রূপরেখা
ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার এই চিত্র থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সংবিধান সংস্কার কমিশন বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন প্রস্তাব করে।
এই প্রস্তাবনাগুলোকে মূলত তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়: নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা এবং প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত ক্ষমতা সংক্রান্ত বিধান।
নির্বাহী বিভাগের সংস্কার
- জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি) গঠন: বিদ্যমান নিয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তে, কমিশন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগের জন্য নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা ও বিচার বিভাগের সমন্বয়ে একটি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি) গঠনের প্রস্তাব করেছিল। এই কাউন্সিল নির্বাচন কমিশন (ইসি), পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি), অ্যাটর্নি জেনারেলসহ গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদগুলোতে নিয়োগ দেবে বলে প্রস্তাব করা হয়। তবে বিএনপিসহ কিছু রাজনৈতিক দলের জোরালো আপত্তির কারণে এই প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত বাদ দেওয়া হয়। বিএনপির যুক্তি ছিল, এই ধরনের কাউন্সিল করা হলে নির্বাহী বিভাগ দুর্বল হয়ে যাবে এবং সরকারের কর্তৃত্ব থাকবে না ।
- রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি: প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা হ্রাস এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট পদে রাষ্ট্রপতিকে সরাসরি নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। এর মধ্যে মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন, প্রেস কাউন্সিল এবং আইন কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোতে রাষ্ট্রপতি কারও পরামর্শ বা সুপারিশ ছাড়াই নিজ এখতিয়ারে নিয়োগ দিতে পারবেন বলে সিদ্ধান্ত হয় । তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ও এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে নিয়োগের ক্ষমতা সরাসরি রাষ্ট্রপতির হাতে দেওয়ার বিষয়ে বিএনপি-সহ ৬টি দল ও জোট আপত্তি জানায়।
আইনসভা ও সংসদীয় সংস্কার
- দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ: সংসদকে আরও কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক করতে কমিশন দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ গঠনের সুপারিশ করে। নিম্নকক্ষ ৪০০ আসন নিয়ে গঠিত হবে, যার মধ্যে ১০০টি আসন সরাসরি ভোটে নির্বাচিত নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। উচ্চকক্ষে ১০৫টি আসন থাকবে, যার মধ্যে ১০০টি আসন আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতিতে এবং বাকি ৫টি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হবেন । তবে বিএনপি আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির বিরোধিতা করে এবং নিম্নকক্ষে প্রাপ্ত আসনের অনুপাতে উচ্চকক্ষে আসন বণ্টনের পক্ষে মত দেয়।
- ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন: সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদটি সংসদের কার্যকারিতা নষ্ট করে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করেছে বলে সমালোচিত। ঐকমত্য কমিশন এই অনুচ্ছেদ সংশোধনের প্রস্তাব করে। সিদ্ধান্ত হয় যে, অর্থবিল ও আস্থা ভোট ছাড়া অন্য যেকোনো বিষয়ে সংসদ সদস্যরা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবেন । এটি সংসদ সদস্যদের দলীয় হুইপের বাইরে গিয়ে ভিন্নমত প্রকাশের সীমিত স্বাধীনতা দেবে।
- সংসদীয় কমিটির সভাপতি: প্রধানমন্ত্রীর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি হিসাব, অনুমিত হিসাব, বিশেষ অধিকার ও সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি-সহ চারটি গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় কমিটির সভাপতি পদে বিরোধী দল থেকে নির্বাচন করার বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন
- মেয়াদসীমা ও পদ বিভাজন: একজন ব্যক্তি জীবনে সর্বোচ্চ ১০ বছর প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে পারবেন, এই বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য হয়েছে । তবে একই ব্যক্তি একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধানের পদে থাকতে পারবেন না—এমন একটি প্রস্তাব আনা হলে বিএনপি-সহ কয়েকটি দল তাতে ভিন্নমত দেয়। তাদের যুক্তি ছিল, সংসদীয় গণতন্ত্রে এটি একটি দলের গণতান্ত্রিক অধিকার ।
- জরুরি অবস্থা জারির প্রক্রিয়া: জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য ‘প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষরের’ পরিবর্তে ‘মন্ত্রিসভার অনুমোদনের’ বিধান যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে । জরুরি অবস্থা ঘোষণা–সম্পর্কিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিরোধীদলীয় নেতা অথবা তার অনুপস্থিতিতে বিরোধীদলীয় উপনেতার উপস্থিতি অন্তর্ভুক্ত করারও প্রস্তাব আছে।
ঐকমত্য ও ভিন্নমতের দেয়াল: রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান বিশ্লেষণ
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংলাপ প্রক্রিয়া থেকে বোঝা যায়, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমঝোতা হলেও, মৌলিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভিন্নমত বিদ্যমান। এই ভিন্নমতগুলো শুধুমাত্র আদর্শগত বিরোধ নয়, বরং এর পেছনে গভীর রাজনৈতিক কৌশলও কার্যকর রয়েছে।
ঐকমত্যের ক্ষেত্রগুলো তুলনামূলকভাবে কম বিতর্কিত এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মূল লক্ষ্যকে সরাসরি প্রভাবিত করে না। যেমন, একজন ব্যক্তি জীবনে সর্বোচ্চ ১০ বছর প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে পারবেন, এই প্রস্তাবে সব দল একমত হয়েছে । একইভাবে, অর্থবিল ও আস্থা ভোট ছাড়া অন্য যেকোনো বিষয়ে সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা সংক্রান্ত ৭০ অনুচ্ছেদের আংশিক সংশোধনেও ঐকমত্য হয়েছে । ইসি গঠনে একটি বাছাই কমিটির প্রস্তাবটিও ঐকমত্যে পরিণত হয়েছে, যা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে কিছুটা সীমিত করবে।
তবে বিএনপির ভিন্নমত থাকা প্রস্তাবগুলো সংস্কারের মূল উদ্দেশ্যকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি) গঠনের প্রস্তাবটি ছিল নির্বাহী বিভাগ থেকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে পৃথক করার একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ। কিন্তু বিএনপির আপত্তির কারণে এটি বাতিল হয়ে যায় । বিএনপির যুক্তি ছিল যে, এমন একটি কমিটি গঠন করা হলে নির্বাহী বিভাগ দুর্বল হয়ে যাবে এবং সরকারের কর্তৃত্ব থাকবে না। তবে এই যুক্তির পেছনে একটি গভীর রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ থাকতে পারে। যদি বিএনপি ভবিষ্যতে ক্ষমতায় আসে, তাহলে তারা প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যমান ক্ষমতাগুলো ভোগ করতে চাইবে। এনসিসি বা কমিটি গঠনের মতো প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করলে তাদের ক্ষমতা সীমিত হয়ে আসবে। তাই, এই ভিন্নমত আদর্শগত নয়, বরং ক্ষমতা ধরে রাখার রাজনৈতিক কৌশল বলে মনে করা হয়।
একইভাবে, একই ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধানের পদে না থাকার প্রস্তাবটিতেও বিএনপি আপত্তি জানায় । তাদের যুক্তি ছিল যে, এটি একটি দলের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি । এই ভিন্নমতটি আবারও ক্ষমতা-কেন্দ্রিক রাজনৈতিক অবস্থানের ইঙ্গিত দেয়। একইভাবে, সংসদের উচ্চকক্ষে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতির বিরোধিতা করে বিএনপি নিম্নকক্ষে প্রাপ্ত আসনের অনুপাতে উচ্চকক্ষে আসন বণ্টনের পক্ষে মত দেয়। এই অবস্থানও তাদের ভবিষ্যৎ ক্ষমতার হিসাব-নিকাশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।
এই কৌশলগত ভিন্নমতগুলো প্রমাণ করে যে, রাজনৈতিক দলগুলো জনস্বার্থের চেয়ে দলীয় স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে, যা একটি সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য বড় বাধা। এই ভিন্নমতের দেয়ালগুলো সংস্কার প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে দিয়েছে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ পরিবর্তনকে বাধাগ্রস্ত করেছে।
প্রস্তাবিত সংস্কারের কার্যকারিতা ও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা
ঐকমত্যে পৌঁছানো প্রস্তাবনাগুলো কি আদৌ প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র ক্ষমতা কমাতে কার্যকর হবে? প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, এই পরিবর্তনগুলো সীমিত এবং প্রতীকী। ঐকমত্য কমিশন নিজেই স্বীকার করেছে যে, যতটুকু ঐকমত্য হয়েছে, তাতে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা "খুব সামান্যই কমবে"। ইসি গঠনে বাছাই কমিটির বিধান যুক্ত হলেও, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদ, যেমন পিএসসি, সিএজি ও দুদকে নিয়োগের পদ্ধতি অপরিবর্তিত থাকছে। রাষ্ট্রপতির হাতে যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের (যেমন মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন) নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সেগুলো প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন আনবে না।
ভিন্নমতের অনিশ্চয়তা এই প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করেছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আলোচনার ফলাফল হিসেবে 'জুলাই সনদ'-এর যে খসড়া রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো হয়েছে , তার কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। যেহেতু বিএনপিসহ কয়েকটি দল তাদের ভিন্নমতের কথা প্রকাশ্যে জানিয়েছে এবং এগুলোকে তাদের আগামী নির্বাচনের ইশতেহারে রাখার ঘোষণা দিয়েছে , তাই ভবিষ্যতে তারা ক্ষমতায় এলে এই সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবে না । এই বাস্তবতা সংস্কারের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি বড় ধরনের অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে।
ঐকমত্য কমিশন কি আসলে একটি ‘দুর্বল’ উপসংহারে পৌঁছতে বাধ্য হয়েছে, নাকি এটি একটি কৌশলগত আপোষ? এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। যদি সংস্কারের উদ্দেশ্য সত্যিই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হতো, তাহলে এনসিসি, পিআর, বা প্রধানমন্ত্রীর পদ বিভাজনের মতো মৌলিক প্রস্তাবগুলোতে ভিন্নমত থাকত না। ঐকমত্য কেবল তুলনামূলকভাবে কম বিতর্কিত বা দলগুলোর জন্য সুবিধাজনক বিষয়গুলোতে হয়েছে। এটি থেকে বোঝা যায় যে কমিশন একটি রাজনৈতিক আপোষ করতে বাধ্য হয়েছে, যা একটি গভীরতর সংস্কারের পরিবর্তে একটি সাময়িক স্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা করেছে। এটি গণতন্ত্রের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের জন্য একটি বড় ঝুঁকি।
তুলনামূলক বিশ্লেষণ: আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ক্ষমতা ও ভারসাম্য
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণকে একটি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তুলনা করলে এর অনন্যতা আরও স্পষ্ট হয়। বিশ্বের অনেক সংসদীয় গণতন্ত্রেও সরকারপ্রধান শক্তিশালী, কিন্তু তাদের ক্ষমতা সাধারণত সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতার মাধ্যমে সীমিত করা হয়।
- যুক্তরাজ্য: ব্রিটিশ সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারের প্রধান এবং তার দল পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে তিনি কার্যত নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করেন । তিনি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারেন এবং সরকারি নীতি নির্ধারণে তার প্রভাব অপরিসীম । তবে বিচারপতি নিয়োগের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে এখন স্বাধীন সংস্থাগুলোর সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয় । যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী একই সাথে দলের প্রধানও থাকেন । তবে, সেখানে কঠোর দলীয় হুইপ থাকলেও সংবিধানের মতো ৭০ অনুচ্ছেদের কোনো বিধান নেই।
- ভারত: ভারতের প্রধানমন্ত্রীও অত্যন্ত শক্তিশালী। তিনি মন্ত্রিপরিষদের প্রধান, লোকসভার নেতা এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান । তিনি মন্ত্রী নিয়োগ, দফতর বণ্টন এবং সরকারের নীতি নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তবে, ভারতের সংবিধানে ক্ষমতাকে রাষ্ট্রপতি, লোকসভা (নিম্নকক্ষ) এবং রাজ্যসভার (উচ্চকক্ষ) মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণভাবে বন্টন করা হয়েছে।
- জার্মানি: জার্মানির শাসনব্যবস্থা বাংলাদেশের মতো সংসদীয় হলেও, এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো চ্যান্সেলর (প্রধানমন্ত্রী) এবং রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার স্পষ্ট বিভাজন। চ্যান্সেলর হলেন নির্বাহী বিভাগের প্রধান , আর রাষ্ট্রপতি হলেন রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক প্রধান। জার্মান চ্যান্সেলরেরও ব্যাপক ক্ষমতা রয়েছে, তবে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে তাকে কাজ করতে হয়।
এই তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে, অন্যান্য সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রী শক্তিশালী হলেও, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মতো এতটা কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা সাধারণত দেখা যায় না । সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগের ওপর প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণ, এবং একই সাথে সরকার, সংসদ ও দলের প্রধানের পদে থাকার কারণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা প্রায় নিরঙ্কুশ। এই পরিস্থিতিটি ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।
পর্যালোচনা ও উপসংহার: পথচলার বাধা ও প্রত্যাশা
সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য ও ভিন্নমতের বিশ্লেষণ থেকে এটি স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা একটি জটিল ও দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। যদিও কিছু বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে, যেমন প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদসীমা নির্ধারণ এবং ইসি গঠনে নতুন পদ্ধতি, এই পরিবর্তনগুলো সংস্কারের মূল লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে।
এই প্রক্রিয়াটি একটি ‘দুর্বল’ সংস্কারের পথ নির্দেশ করে, যা মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তনের পরিবর্তে রাজনৈতিক আপোষকে প্রাধান্য দিয়েছে। জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি), আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) এবং প্রধানমন্ত্রীর পদ বিভাজনের মতো মৌলিক প্রস্তাবগুলোতে ভিন্নমত থাকা ইঙ্গিত দেয় যে রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের চেয়ে ক্ষমতাকে ধরে রাখার বিষয়ে বেশি আগ্রহী।
ভবিষ্যতে নির্বাচিত সরকার, বিশেষ করে যেসব দল ভিন্নমত দিয়েছে, তাদের পক্ষে এই প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন করার কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে, একটি গণতান্ত্রিক, জবাবদিহিমূলক এবং ভারসাম্যপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সাংবিধানিক পরিবর্তনই যথেষ্ট নয়। রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং জনগণের পক্ষ থেকে অব্যাহত চাপও অপরিহার্য।
গণতন্ত্রকে টেকসই করতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোকে শুধুমাত্র দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। সংবিধান সংস্কার প্রক্রিয়াটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচনা হলেও, এটি একটি 'পূর্ণাঙ্গ সমাধান' থেকে অনেক দূরে। এখন দেখার বিষয়, দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক নেতৃত্ব এই সীমিত ঐকমত্যের ওপর ভিত্তি করে আরও বড় সংস্কারের পথে এগিয়ে যায়, নাকি ভিন্নমতের দেয়ালগুলো স্থায়ীভাবে গণতন্ত্রের পথকে রুদ্ধ করে দেয়।
নিউজবাংলাদেশ.কম/পলি






































